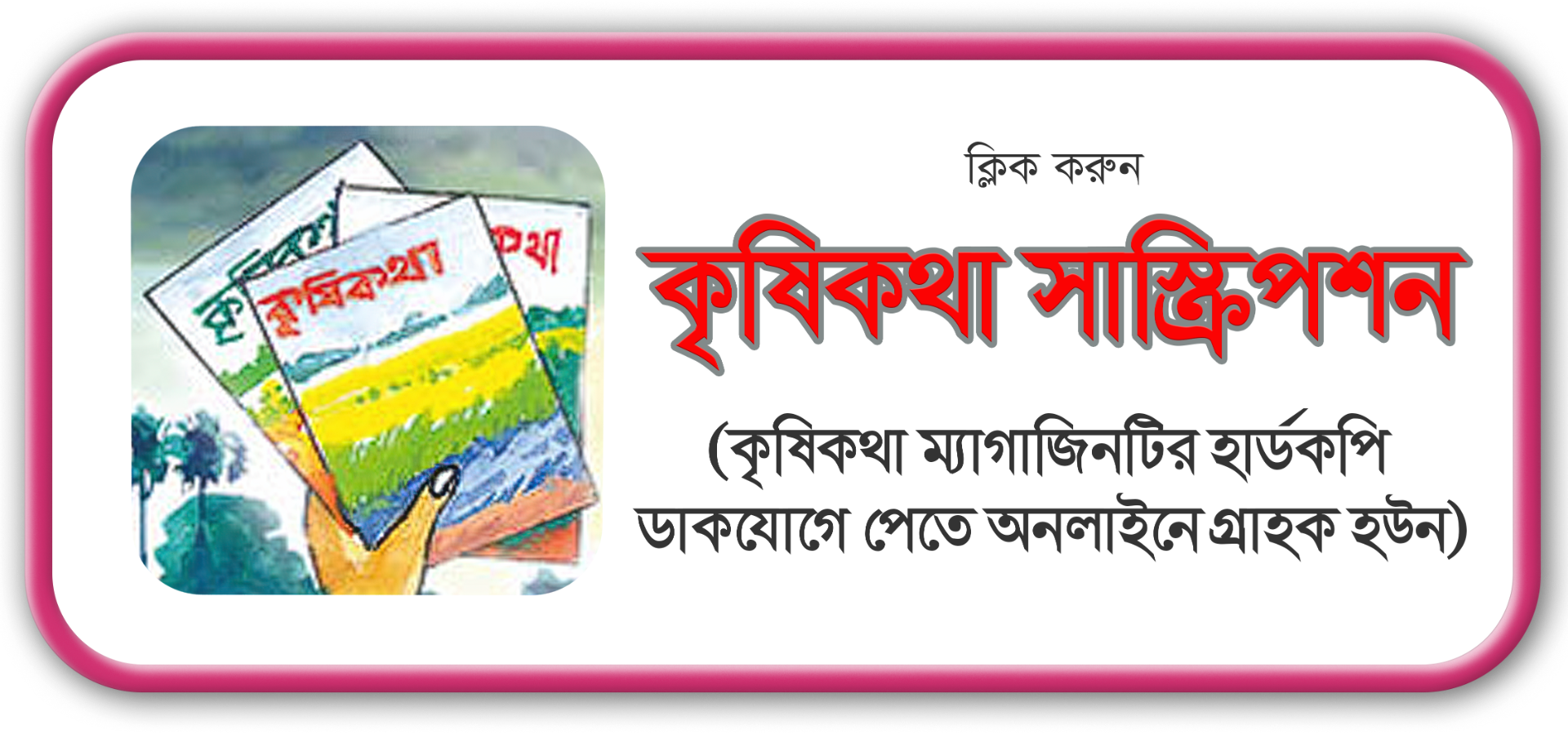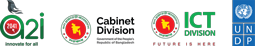বদলে যাচ্ছে কৃষিজ সংস্কৃতি

সংস্কৃতি শব্দটির আভিধানিক অর্থ সংস্কার, উন্নয়ন, অনুশীলন ইত্যাদি। আবার সংস্কৃতির সুন্দর সমার্থক শব্দ হচ্ছে কৃষ্টি, কর্ষণ। মোট কথা সংস্কৃতিকে যদি সোজাসাপটাভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হলে বলতে হবে যাপিত জীবনের প্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশ, যা আমাদের চেতনাকে নাড়া দেয় বা এ দুইয়ের মধ্যে বাস করে আমরা যা করছি সেটাই আমাদের সংস্কৃতি।
আবার যে পরিবারে বাস করছি সে পরিবারে সাধারণ কিছু কৃষ্টি কালচার থাকে, যা ওই পরিবারের সংস্কৃতি। এভাবে সমাজ, অঞ্চল, রাষ্ট্রে, ধর্মে-কর্মে এবং জাতিভেদে সংস্কৃতির ভিন্নতা দেখা যায়। দিনের পরে রাত, রাতের পরে দিন। মানুষ এগিয়ে চলে সামনের দিকে, জন্ম নেয় নতুন কৃষ্টির নতুন সভ্যতার। কাজেই পয়লা বৈশাখে চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রা বা রমনা বটমূল থেকে যদি বলা হয় আমরা বাঙালি সংস্কৃতির উদযাপন করছি, তাহলে বলব কথাটি পুরোপুরি সত্য নয়। আসলে এটি হচ্ছে ফেলে আসা সংস্কৃতির আংশিক স্মৃতিচারণ মাত্র। কেননা সংস্কৃতি হচ্ছে বহতা নদীর মতো বহমান।
সে যা হোক। সংস্কৃতির বিবর্তন আমার বিষয় নয়। বিষয়টা হচ্ছে আমাদের কৃষিজ সংস্কৃতি তথা গ্রামীণ সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘কৃষিই কৃষ্টি’। রবীন্দ্র যুগের এমন উক্তি সত্যই খাঁটি। কারণ তখনও প্রসার লাভ করেনি শহুরে সংস্কৃতি, ছোঁয়া লাগেনি আধুনিক কৃষির। কিন্তু কালক্রমে আধুনিকতার ছোঁয়া তথা বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনে কৃষি ও কৃষক সমাজে এসেছে পরিবর্তন। জন্ম নিয়েছে নতুন সংস্কৃতির, নতুন সভ্যতা।
ধরা যাক খাদ্য সংস্কৃতির কথা। যেই কৃষক সকালের নাশতায় পান্তা ভাত আর কাঁচামরিচ জঠরে ঢুকিয়ে ছুটে যেত তার প্রিয় কর্মস্থল আবাদ ভূমিতে। এখন কৃষক সমাজে তেমনটি আর খুব দেখা যায় না। গ্রামীণ তথা কৃষক সমাজে শীতকালের পিঠে পায়েস থেকে আরম্ভ করে সব রকমের মিষ্টি জাতীয় খাদ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, খেজুরের রস বা খেজুরের পাটালি গুড়। আজকাল এ অকৃত্রিম খাদ্য সংস্কৃতির ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। কারণ বহুবিধ তার মধ্যে জ্বালানি ও গাছির অভাব অন্যতম। ফলে নতুন করে আর খেজুর গাছ রোপিত হচ্ছে না। যাও আছে তার থেকে যতটুকু গুড় আসে তাও ভেজাল। বেশির ভাগ জায়গায়ই ১ ভাগ খেজুরের গুড়ের সাথে ৩ ভাগ চিনি মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে ভেজাল গুড়। তাছাড়া নগর সংস্কৃতির ঢেউ গ্রামীণ জীবনেও লাগতে শুরু করেছে। ফলে অতিথি আপ্যায়নে ব্যবহৃত হচ্ছে বিস্কুট, চানাচুর, নুডলস, চা ইত্যাদি। অথচ কী স্বকীয়তাই না ছিল আমাদের গ্রামীণ তথা কৃষক সমাজের খাদ্য সংস্কৃতিতে। আমাদের লোকজ কবির পঙ্ক্তিমালায় ফুটে উঠত চিরায়ত খাদ্য সংস্কৃতির কথা।
‘আমার বাড়ী যাইও বন্ধু বসতে দেব পীড়ে
জল পান করিতে দেব শাইলী ধানের চিঁড়ে।
শাইলী ধানের চিরে নয় বিন্নী ধানের খই
সংগে আছে কালো গরুর গামছা পাতা দই।’
কৃষাণ বধূর গয়নাতে এসেছে পরিবর্তন। এক সময় কৃষাণ বধূ/মেয়েদের পায়ে রুপার নূপুর বা খারু, কোমরে রুপার বিছা, হাতে রেশমি চুড়ি, হাতের একদম উপরে রুপার বাগ, গলায় পুতির মালা বা রুপার মালা বা হাঁসুলি, নাকে নথ ইত্যাদি। কপালে লাল টিপ আর বাহারি গয়নায় কৃষাণ বধূরা যখন গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে চলে যেত বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর গৃহে কিংবা স্বামীর গৃহ থেকে বাবার বাড়ি তখন নূপুরের ছন্দে কবি খুঁজে পেত কাব্যিক ছন্দ। জসিমউদ্দীন তার নকশি কাঁথার মাঠ কাব্যে যৌবনবতী এক গ্রাম্য মেয়ের পায়ের গয়নার এক বড় অনুষঙ্গ নূপুরের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-
‘কেউ বা বলে আদ্যিকালের এই গাঁর এক চাষী
ওই গাঁর এক মেয়ের প্রেমে গলায় পরে ফাঁসী
এ পথ দিয়ে একলা মনে চলছিল ঐ গাঁয়ে
ও গাঁর মেয়ে আসছিল সে নূপুর পরা পায়ে।’
কবি তার কবর কবিতায় কৃষাণ বধূর পুতির মালা এবং নাকের নথ নামক গয়নার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,
‘শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু’পয়সা করি দেড়ি
এক ছড়া পুতির মালা নিতে কখনও হতো না দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া ঘাটে
সন্ধ্যে বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুর বাড়ীর বাটে।
হেসো না হেসো না শোন! দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে
দাদু যে তোমার কত খুশী হতো দেখতিস যদি চেয়ে।
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া এতদিন পরে এলে
আমি যে হেথায় পথ পানে চেয়ে কেদে মরি আঁখি জলে।’
গয়না সংস্কৃতির পরিবর্তনের ফলে উল্লিখিত গয়নার তেমন প্রচলন আর দেখা যায় না। ক্রমবর্ধমান দানাজাতীয় খাদ্যশস্যের চাহিদা মেটাতে গিয়ে কুসুম ফুল, গুজিতিল, তিসি, চিনা কাউন, বোনা আমন, বোনাআউশ এ জাতীয় শস্যের আবাদ আশঙ্কাজনক হারে কমে গিয়েছে। আবার এদের মধ্যে কোনো কোনো ফসলের আবাদের বিলুপ্তি ঘটেছে। অথচ এসব ফসলে যখন মাঠ ভরে থাকতো তখন প্রকৃতি সাজতো অপরূপ সাজে। গ্রীষ্মের দামাল বাতাস যখন বয়ে যেত বিস্তীর্ণ শস্যের ওপর দিয়ে তখন মনে হতো ধান কাউনের শস্যের জমি যেন ঢেউ খেলানো পানিবিহীন অনবদ্য প্রসারিত নদী। মাঠের পরে মাঠ শস্যের এ যে সমাহার তা দেখে কবির মনকে নাড়া দিয়েছিল। কবি লিখেছেন,
“এই এক গাঁও ঐ এক গাঁও মধ্যে ধু-ধু মাঠ
ধান কাউনের লিখন লিখা করছে সদা পাঠ।”
ঠিক একই চিত্র ডালজাতীয় শস্যের ক্ষেত্রেও। তার মধ্যে মটরশুঁটির আবাদ এখন আর উল্লেখ করার মতো তেমন কিছু নেই। অথচ আমাদের পল্লী কবি মটরশুঁটির কথা উল্লেখ করে তার শহুরে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছে এভাবে,
‘তুমি যদি যাও দেখিবে সেথায় মটর লতার সনে
শীম আর শীম হাত বাড়ালেই মুঠি মুঠি ভরে সেই ক্ষণে
তুমি যদি চাও সে সব কুড়ায়ে
নারার আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে
খাব আর যত গেয়ো চাষীদের ডাকিয়া নিমন্ত্রণে’
কৃষক সমাজে চাষাবাদের যে হাতিয়ার সেই কৃষি যন্ত্রপাতিতেও এসেছে পরিবর্তন। আমাদের পল্লী কবি জসিমউদদীনের কবিতায় চির চেনা প্রধানতম যন্ত্রটির কথা উঠে এসেছে এভাবে,
‘সোনালী উষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
লাঙ্গল লয়ে ক্ষেতে ছুটিতাম গায়েরও পথ ধরি’
আধুনিক যন্ত্রপাতির ভিড়ে চিরচেনা সেই লাঙল জোয়াল আর দেখা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। অথচ নানাবিধ কারণে তার ব্যত্যয় ঘটছে। যেমন- ধরা যাক আমাদের উল্লেখযোগ্য ঋতু বর্ষার কথা। উজানের পানি প্রত্যাহার, নদীর তলদেশ ভরাট, বিভিন্ন প্রকার অপরিকল্পিত সড়ক ব্যবস্থার ফলে বর্ষা তার চিরন্তন রূপ হারিয়ে ফেলেছে। বর্ষা হয় না, হলেও তা রূপ নেয় সর্বগ্রাসী বন্যায়। অথচ নদীমাতৃক এই দেশে বর্ষার প্রভাব গ্রামীণ তথা কৃষক সমাজকে ভিন্ন মাত্রা যোগ করত। মহাজনী ধান-পাটের পাল তোলা নৌকা, নায়রির এক মাল্লাইয়া ছৈওয়ালা নৌকা, আষাঢ়ের খরস্রোতা নদী, আউশ ধানসহ চিত্র বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ হতো। ছুঁয়ে যেত কবি মনকেও। বর্ষার যে উচ্ছ্বল যৌবন প্লাবি সুন্দর একটি রূপ আছে তা ফুটে উঠেছে আমাদের বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাপ্তি গল্পে- ঠিক এভাবে,
“অপূর্ব কৃষ্ণ বি,এ পাশ করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছিল। নদীটি ক্ষুদ্র বর্ষার অন্তে শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একে বারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশ ঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে। বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘ মুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে। নৌকায় আসীন অপূর্ব কৃষ্ণের মনের ভিতরকার ছবি যদি দেখিতে পাইতাম, তন্দ্রে দেখিতাম সেখানেও এই যুবকের মানস নদী নববর্ষার কুলে ভরিয়া আলোকে জ্বল জ্বল বাতাসে ছলছল করিয়া উঠিতেছে।”
কবি গুরু অন্যত্র আষাঢ় ও আউশ ক্ষেতের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,
‘সারা দিন ঝরে ঝর ঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভরে ভর।’
আগেই বলেছি উফশী জাত প্রবর্তনের ফলে আমাদের স্থানীয় জাতের বিলুপ্তি ঘটতে চলেছে। তার জ্বলজ্বলে উদাহরণ আমাদের স্থানীয় জাতের আউশ ধান। অথচ আষাঢ় এবং আউশ ধান ছিল স্বভাব কবির মানস পটের মনোমুগ্ধকর ছবি। যৌবনবতী আষাঢ়ের পানি প্রবেশ করত ফসলি জমিতে। সারা পড়ে যেত আউশ ধান কাটার। কখনও থেমে থেমে কখনও বা অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরত সারা দিন ধরে। কৃষক বৃষ্টি উপেক্ষা করে মাথাল মাথায় ধান কাটতো আপন মনে। জলজ পাখি পানকৌড়ি নিরন্তর ডেকে যেত টুব্ টুব্ করে। কৃষাণের কণ্ঠে ভেসে উঠত ধুয়া, মুর্শিদী, ভাটিয়ালিসহ আরও কত গানের সুর। জলজ পাখির ডাক আর কৃষকের প্রাণ খোলা গানের মূর্ছনা ছড়িয়ে যেত দিগন্ত জুড়ে। সব মিলিয়ে এ যে কাব্যিক মুহূর্ত, এই যে কাব্যময়তার অন্তর প্লাবি আবেগ তা কবির মন হকচকিত করে দিত।
যেহেতু জীবন বহতা নদীর মতো বয়ে চলা এক নদী। এর বাঁকে বাঁকে সৃষ্টি হয় কত আখ্যান। মন পবনের নাও ভাসিয়ে ফিরে যেতে চায় ফেলে আসা বাঁকের আখ্যানে। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ জীবন চলে জীবনের নিয়মে।
মো. আনোয়ার হোসেন*
* উপসহকারী কৃষি অফিসার, মানিকগঞ্জ সদর, মোবাইল : ০১৭১৩৫২৯৭০৭