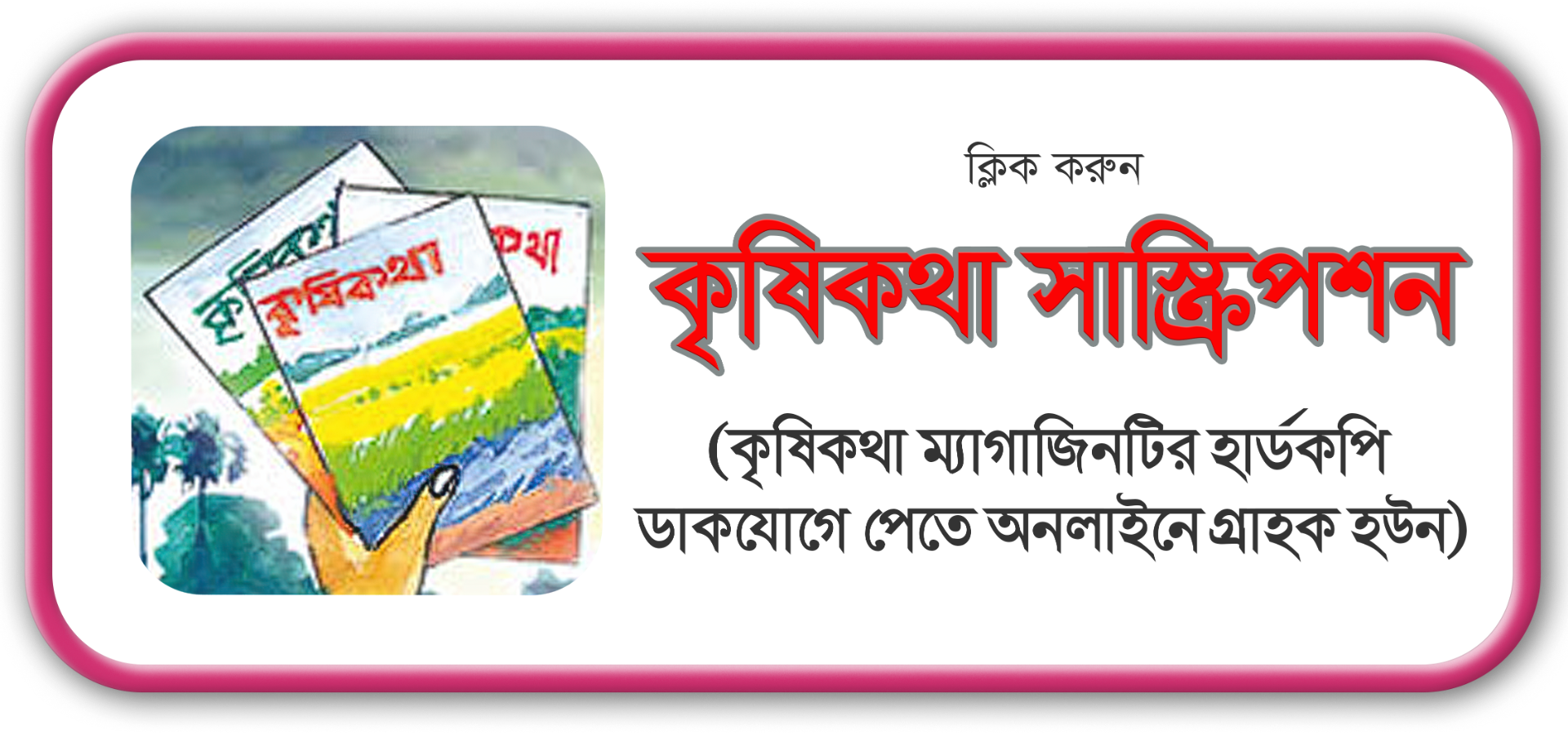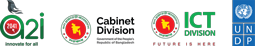দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী বিএআরআই প্রযুক্তি

পরিবর্তিত জলবায়ুগত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিপ্রবণ অবস্থানে আছে যার মধ্যে কৃষি খাত অন্যতম। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান প্রভাবগুলো হলো- মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, বন্যা, জলমগ্নতা, উপকূলীয় বন্যা, খরা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- সাইক্লোন, সিডর, আইলা, মহাসেন, জলোচ্ছ্বাস। উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় ফসল, ভৌত-অবকাঠামো, গাছপালা, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি ধ্বংস করে এমনকি মানুষের জীবনহানী ঘটায়। পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় তুলনামূলকভাবে বেশি। বাংলাদেশের প্রায় ৩০ শতাংশ নিট চাষযোগ্য ভূমি উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু এ এলাকার সব ভূমি মূলত মাটির লবণাক্ততা ও জোয়ারের কারণে ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত করা সম্ভব হয় না। সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ০.৮৪ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা রয়েছে। গত চার দশকে (১৯৭৩-২০০৯) দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ২৭ শতাংশ এলাকা এবং অন্যদিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ৬৯.৫২ শতাংশ নতুন এলাকায় বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটেছে (ঝজউও, ২০১০)। এতে ফসল উৎপাদন মারাত্মভাবে ব্যাহত হয় যা দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে বড় বাধা। এছাড়াও দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ১.৮২ লাখ হেক্টর চরাঞ্চল আছে যা সাধারণত রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে চাষের অনুপযোগী থাকে। কারণ রবি মৌসুমে মাটিতে যথেষ্ট রসের অভাব থাকে এবং খরিফ ১ মৌসুমে আগাম জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়।
নিচু এবং অতি নিচু এলাকাগুলো উপকূলীয় বন্যা ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে জুন থেকে ডিসেম্বর এমনকি সারা বছর জমি জলমগ্ন-পতিত থাকে। উপকূলীয় বন্যা ও লবণাক্ততার কারণে পানি নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পোল্ডারের ভেতরের ফসল রক্ষা পেলেও এর বাহিরে চাষকৃত ফসলগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়। আবার অসময়ে বৃষ্টিপাত বা জোয়ারের পানি নামতে দেরি হলেও রোপা আমন ধান কাটার পর শীতকালীন ফসল সময়মতো বপন-রোপণ করা যায় না। অন্যদিকে শীতের দীর্ঘতা কম থাকায় সাধারণত শীতকালীন ফসল গম, আলু, শীতকালীন শাকসবজি, সরিষার উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় বা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয় না। এতে অনেক কৃষক শীতকালীন ফসল উৎপাদন করা থেকে বিরত থাকে ফলে জমি পতিত থাকে। পরিবর্তিত জলবায়ুর ফলে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ ও ফসলভিত্তিক ক্ষতির তীব্রতা দেখা যায়। এতে ফসলের উৎপাদনশীলতা কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাগুলো লবণাক্ততা, বন্যা, জলমগ্নতা, খরার কারণে গড়ে প্রায় ৩১.০০ শতাংশ (২৯.৪৫ শতাংশ রবি, ৫৫.১০ শতাংশ খরিফ-১ এবং ৮.৪৫ শতাংশ খরিফ-২ মৌসুমে) জমি পতিত থাকে। এ কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চল, যা এক সময় বাংলার শস্যভা-ার হিসেবে বিবেচনা করা হতো তা বর্তমানে স্বল্প কৃষি উৎপাদন অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে। এর আগে পরিচালিত গবেষণা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবের ফলে ভবিষ্যতে এ অবস্থার আরও অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ অবস্থায় পরিবর্তীত জলবায়ুগত পরিস্থিতিতে অভিযোজনের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতির জন্য গবেষণার মাধ্যমে স্থানভিত্তিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা আবশ্যক।
জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইঅজও বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার অভিযোজনের উপযোগী দানাজাতীয়, ডাল, তেলবীজ, কন্দাল, শাকসবজি, ফল, মসলা ফসলের আধুনিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ফসলের আধুনিক জাতগুলো হলোÑ বারি গম-২৫ বারিগম ২৫, ২৯, ৩০ বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯, ১২, ১৩; বারি বার্লি-৫,৬; বারি কাউন-২, ৩; বারি সয়াবিন-৫, ৬; বারি সরিষা-১১, ১৬; বারি চিনাবাদাম- ৮, ৯; বারি তিল-৪; বারি সূর্যমুখী-২; বারি মুগ-৬, ৭, ৮; বারি খেসারি-২, ৩; বারি ফেলন-১, ২; বারি আলু-১২; ৭২,৭৩; বারি মিষ্টিআলু-৬, ৭, ৮, ৯; বারি পানিকচু- ২, ৩; বারি টমেটো-১৪, ১৫; বারি বিটি বেগুন-২; বারি মাল্টা-১; বারি পেয়ারা-২; বারি আমড়া-১, ২;বারি নারিকেল-১, ২; বারি সুপারি-১, ২।
হাইস্পিড রোটারি টিলার : বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আমন ধান কাটার পর রবিশস্য চাষ করতে কৃষকের প্রায় ডিসেম্বর মাস এমনকি জানুয়ারি লেগে যায়। হাইস্পিড রোটারি টিলার দিয়ে ১-২টি চাষ দিয়ে কম সময়ে জমি তৈরি করে জমিতে ফসল আবাদ করা যায়। এ যন্ত্রের দ্বারা প্রচলিত টিলারের তুলনায় ৫০ শতাংশ সময় ও আর্থিক সাশ্রয় হয়। হাইস্পিড রোটারি টিলারের সাহায্যে শীতকালীন ফসলগুলো সময়মতো বপন করা সম্ভব। যার দ্বারা আমন ধান ও রবি শস্য আবাদের মধ্যকার ব্যবধান কমানো যায়। এতে রবি শস্যে লবণাক্ততা এবং খরা থেকে অনেকটা রক্ষা পাবে।
বেড প্লান্টার : বেড প্লান্টার দিয়ে ১-২টি চাষে বেড তৈরি, সার প্রয়োগ ও বীজ বপনের কাজ একই সাথে করা যায়। এর মাধ্যমে স্থায়ী বেডে বীজ বপন করা যায়। বেডে ফসল করলে সেচ খরচ ও সময় ২৫ শতাংশ কমে, যন্ত্রটি প্রতি ঘণ্টায় ০.১১ হেক্টর জমিতে বেড তৈরি করতে পারে। বেড প্লান্টার দিয়ে গম, ভুট্টা, আলু, মুগ ও তিলসহ বিভিন্ন প্রকার সবজি বীজ বপন করা যায়। স্থায়ী বেডের ক্ষেত্রে দুই ফসলের মাঝের সময় কমিয়ে সময়মতো বীজ বপন সম্ভব হয়। বেড পদ্ধতিতে ফসল ফলালে উৎপাদন খরচ কমে, মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে ও লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন : কেবল পানিতে দ্রবণীয় ইউরিয়া, পটাশ সার এ পদ্ধতিতে তরমুজ, টমেটো, মিষ্টিকুমড়া ফসলে ব্যবহার করা যায়। ফলে সেচ ও সার প্রয়োগ একই সাথে হয়। লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ফার্টিগেশন পদ্ধতি খুবই উপকারী। প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা ৪০-৪৫ শতাংশ সার এবং ৪৫-৫০ শতাংশ পানি কম লাগে। প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন সবজি ফসলের ব্যাকটেরিয়াজনিত নুয়ে পড়া রোগের বিস্তার কম হয়। প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা ২৮-৩০ শতাংশ ফলন বেশি হয়। লবণাক্ত এলাকা যেখানে সেচের পানির অভাব, সেখানে এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা এ পদ্ধতিতে সবজি চাষে ২-২.৫ গুণ বেশি মুনাফা পাওয়া যায়।
এগ্রোফিশারি মিনি পুকুর : এগ্রোফিশারি মিনি পুকুরের আকার হবে ১২ মিটার ঢ ১০ মিটার (বকচরসহ), তবে জলাশয় হবে ১০ মিটার ঢ ৮ মিটার এবং মোট জমির পরিমাণ ২০ মিটার ঢ ১৮ মিটার (৯ শতক)। পুকুরের পাড় হবে ৩ মিটার প্রশস্ত এবং উচ্চতা জমির প্রকৃতির ওপর নির্ভর করবে। তবে জুলাই-আগস্ট মাসে স্বাভাবিক জোয়ারের প্লাবন থেকে কমপক্ষে এক থেকে দেড় ফুট উঁচু রাখতে হবে। বরিশাল-পটুয়াখালী অঞ্চলে যেখানে জোয়ারের প্লাবনের কারণে সময়মতো সবজি চাষ করা যায় না সেখানে বসতবাড়ির পুকুরের পাড় ব্যবহার করে সহজেই সবজি চাষ করা সম্ভব।
কুয়া খনন : লবণাক্ত এলাকায় কুয়া খননের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে রবি ফসল ও সবজি উৎপাদন বেশ সফলতা দেখিয়েছে। ফসলি জমির কাছে ২.৫ মি. (৮ ফুট) লম্বা, ২.৫ মি. (৮ ফুট) চওড়া এবং ১.৮ মি. (৬ ফুট) গভীর কুয়া খনন করে সেচের জন্য মিষ্টিপানি পাওয়া যায় যা দ্বারা এক একর জমির সবজি ফসলের মাদায় সেচ দেয়া যায়। যেহেতু প্রাকৃতিকভাবে মাটির নিচ থেকে মিষ্টি পানি উঠে আসে তাই অন্য কোনো উৎস থেকে পানি লিফটিংয়ের প্রয়োজন হয় না। কুয়ার গভীরতা তেমন বেশি না হওয়ায় পানি তোলার জন্য পাওয়ার পাম্প ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। দেশীয় পদ্ধতিতে অর্থাৎ কলসি, বালতি ব্যবহার করে কুয়ার পানি দ্বারা সহজেই ফসলের মাদায় সেচ দেয়া যায়। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার মাত্রা কমিয়ে সহজেই ফসল উৎপাদন করা যায়।
ভাসমান বেড ও মাচা পদ্ধতিতে (ঋষড়ধঃরহম ইবফ পঁস ঞৎবষষরং: ঋইঞ) শাকসবজি চাষ : সবজি ফসলের বৃদ্ধির ধরন অনুযায়ী কচুরিপানা দিয়ে তৈরি পাশাপাশি দুইটি ভাসমান বেডের মাঝে ৩.০-৬.০ মি. (১০-২০ ফুট) ট্রেলি বা মাচা তৈরির জন্য ফাঁকা রাখা হয়। সবজির চারা ভাসমান বেডে রোপণ করা হয় তবে গাছের শাখা-প্রশাখা ভাসমান বেডের পরিবর্তে মাচায় বেড়ে উঠার যথেষ্ট সুবিধা থাকায় ফলন বেশি হয়। আবার মাচার নিচে ফাঁকা থাকায় ছোট নৌকার মাধ্যমে ফসলের আন্তঃপরিচর্যার কাজও সহজে করা যায়। উদ্ভাবিত ঋইঞ পদ্ধতিতে প্রাথমিক অবস্থায় ভাসমান বেডে স্বল্পমেয়াদি শাকজাতীয় ফসলগুলো উৎপাদন করা যায়। এতে প্রচলিত ভাসমান পদ্ধতির চেয়ে ঋইঞ পদ্ধতিতে শাকসবজির উৎপাদন ও ফসলের নিবিড়তা বাড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, ভাসমান বেড তৈরিতে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ঋইঞ পদ্ধতিতে অর্ধেক কচুরিপানা কম লাগে। ঋইঞ পদ্ধতিতে সহজেই কুমড়াজাতীয় সবজি ও বিভিন্ন শাকজাতীয় লালশাক, বাটিশাক, ধনেপাতা, মুলাশাক, পালংশাক আবাদ করা যায়। ভাসমান বেড ও মাচা পদ্ধতিতে কুমড়া বা লতা জাতীয় উপকূলীয় এলাকায় ¯্রােতবিহীন জলাশয়ে আবাদে উপযোগী।
মাটির লবণাক্ততা প্রশমনে পটাশিয়াম সার : লবণাক্ত মাটিতে পটাশিয়াম প্রয়োগ মাটিতে বিদ্যমান সোডিয়াম আহরনে বাধা দেয়। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্ধারিত মাত্রা অপেক্ষা ২৫-৩০ শতাংশ বেশি পটাশিয়াম প্রয়োগ গাছের জন্য গ্রহণ উপযোগী পটাশিয়ামের প্রাপ্যতা বাড়ায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত ২৫-৩০ শতাংশ পটাশিয়াম ব্যবহার করলে ভুট্টা গাছের ফলন ২০-২৫ শতাংশ বাড়ে। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা প্রশমনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা যায়।
লবণাক্ত এলাকায় মালচ প্রয়োগের মাধ্যমে সবজি চাষ : মালচ মৃত্তিকার আর্দ্রতা সংরক্ষণে সাহায্য করে গাছের মূলাঞ্চল সবসময় ভিজা রাখে। গাছের মূলাঞ্চল থেকে মাটির রসের বাষ্পীভবন কমে। লবণাক্ত মাটির লবণাক্ততা বাড়তে বাধা দেয় এবং গাছের মূলাঞ্চলের লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণে রাখে। গাছে ঘন ঘন সেচ দিতে হয় না ফলে সেচ খরচ কম হয়। অন্যদিকে মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়ন করে। মালচ ব্যবহার করে মৃত্তিকার আর্দ্রতা সংরক্ষণের মাধ্যমে লবণাক্ততা প্রশমন করে বিভিন্ন ফসল আলু, মরিচ, টমেটো, বেগুন, তরমুজ, মিষ্টিকুমড়া চাষ করা যায়।
বিনা চাষে আলু চাষ : বর্ষা বা জোয়ারের পানি নেমে যাওয়ার পর পরই বিনাচাষে আলু চাষ করা যায়। এতে রবি মৌসুমে সময়মতো আলু চাষ করা সম্ভব হয়। মালচিংয়ের জন্য ধানের খড় বা শুকনা কচুরিপানা ব্যবহার করা হয়। জোয়ার-প্লাবন এলাকায় সময়মতো আলু চাষ করা যায় ফলে ফসলের ফলন বাড়ে।
সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ : পুরুষ পোকাকে আকৃষ্ট করার জন্য স্ত্রী পোকা এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নির্গত করে যা সেক্স ফেরোমন নামে পরিচিত। ফাঁদ প্রতি ১ মিলি ফেরোমন একখ- তুলার টুকরায় ভিজিয়ে পানি ফাঁদের প্লাস্টিক পাত্রের মুখ হতে ৩-৪ সেন্টিমিটার নিচে একটি সরু তারের মাধ্যমে স্থাপন করতে হয়। প্রতি বিঘা জমির জন্য ১৫টি ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। চারা লাগানোর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই জমিতে ফেরোমন ফাঁদ পাততে হবে। তবে সেক্স ফেরোমন পোকার ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে। কোনো প্রকার পরিবেশ দূষণ ছাড়াই বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, মরিচ ও কুমড়াজাতীয় সবজি জমিতে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ মথকে ধরে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
বিষটোপ ও রঙিন আঠালো ফাঁদ : বিষটোপ ফাঁদ ব্যবহার হলো ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টিকুমড়া কুচি কুচি করে কেটে তা থেতলিয়ে ০.২৫ গ্রাম মিপসিন ৭৫ পাউডার অথবা সেভিন ৮৫ পাউডার এবং ১০০ মিলিলিটার পানি মিশিয়ে ছোট একটি মাটির পাত্রে রেখে তিনটি খুঁটির সাহায্যে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বিষটোপের পাত্রটি মাটি থেকে ০.৫ মিটার উঁচুতে থাকে। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদ কুমড়াজাতীয় ফসলের জমিতে ক্রমানুসারে ১২ মিটার দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে। এছাড়া হলুদ, সাদা রঙের আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করা যায়। সেক্স ফেরোমন-বিষটোপ-রঙিন আঠালো ফাঁদ যৌথভাবে ব্যবহার করে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে সবজির মাছি, মুগডালের থ্রিপস ও অন্যান্য পোকা দমন করা সম্ভব। তবে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সর্বোচ্চ ফল লাভের জন্য কুমড়াজাতীয় সবজি চাষকৃত সব কৃষককে একত্রে ওই পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করতে হবে।
পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজনের জন্য বারি উদ্ভাবিত আধুনিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ার পাশাপাশি দরিদ্র জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।
ড. মো. আলিমুর রহমান*
ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী**
*ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, রহমতপুর, বরিশাল; **প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরআই, গাজীপুর; বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১