Wellcome to National Portal
কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Text size
A
A
A
Color
C
C
C
C
কৃষি কথা

গবাদি প্রাণীর সদ্যজাত বাছুরের যত্ন ও পরিচর্যা
গবাদি প্রাণীর সদ্যজাত বাছুরের যত্ন ও পরিচর্যা
মোঃ শাহজাহান মিয়া
স্তন্যপায়ী প্রায় সকল প্রাণীর জন্ম প্রক্রিয়া একই হলেও কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে জন্মপরবর্তী নিবিড় যত্ন দরকার হয়। আমাদের দেশে ঘাস আর খড়ের উপর নির্ভর করে পালন করা দেশি গরুর বাছুরের জন্ম পরবর্তী জটিলতা হতো না বললেই চলে কারণ একদিকে গর্ভাবস্থায় গরু যেমন পর্যাপ্ত...
Details
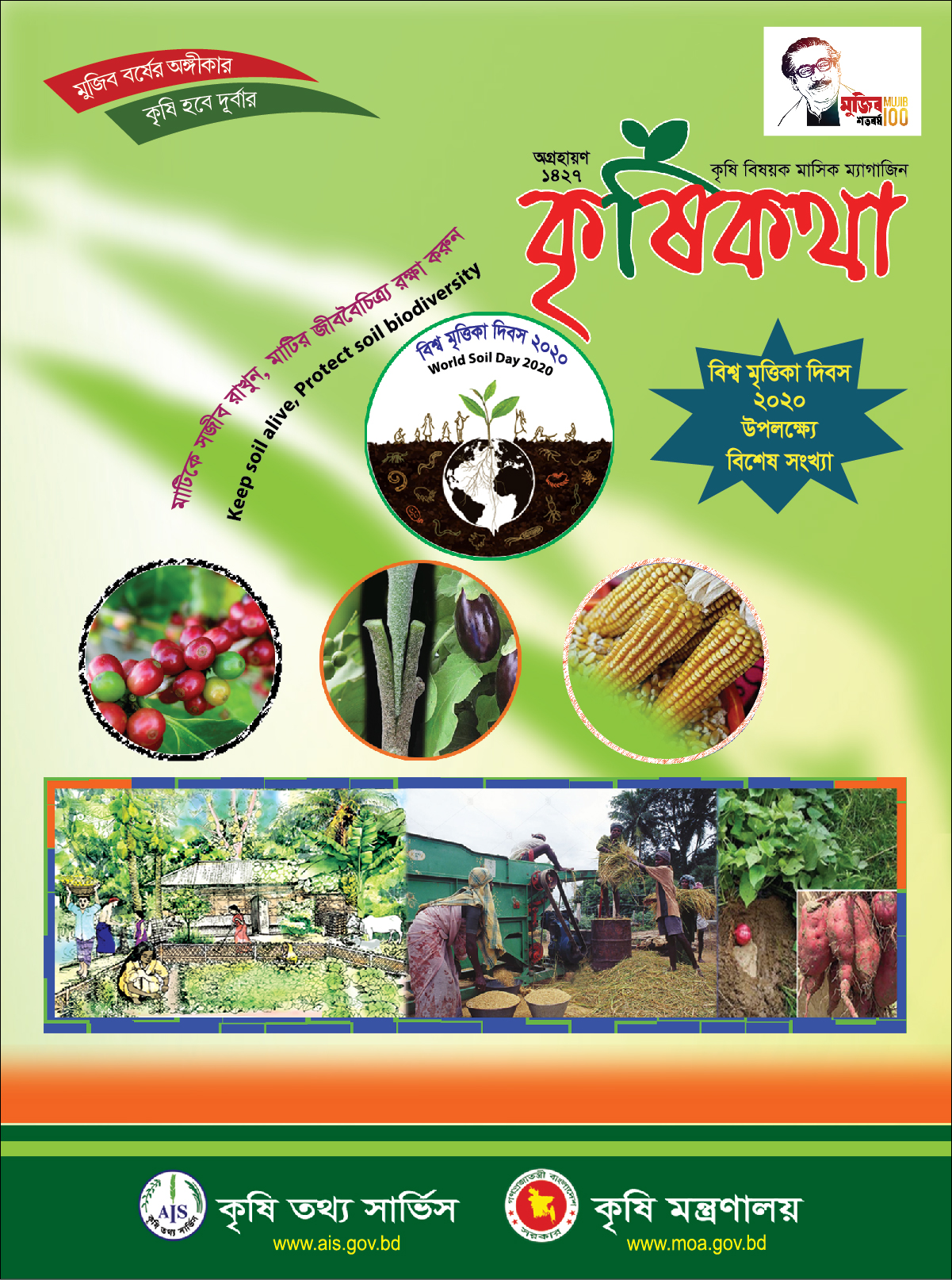
বিলুপ্ত প্রায় মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
বিলুপ্ত প্রায় মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ
মাছ বাঙ্গালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ। দেশে মিঠাপানির ২৬০টি প্রজাতির মাছের মধ্যে ১৪৩ প্রজাতির ছোট মাছ রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে দেশীয় প্রজাতির মাছ আমাদের সহজলভ্য পুষ্টির অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে...
Details

টমেটো ও বেগুনের রোগ দমনে জোড়কলম প্রযুক্তি
টমেটো ও বেগুনের রোগ দমনে জোড়কলম প্রযুক্তি
ড. বাহাউদ্দিন আহমেদ
বেগুন ও টমেটো বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রধান দুটি সবজি। বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বেগুন ও টমেটো চাষের জন্য প্রধান সমস্যা হলো মাটিবাহিত বিভিন্ন রোগ। প্রধানত ঢলেপড়া রোগ ও শিকড়ের গিট রোগ টমেটো ও বেগুন চাষে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। উচ্চ তাপমাত্রা...
Details

বাঙালির নবান্ন উৎসবে সুগন্ধি চাল
কৃষিবিদ ড. মো. আখতারুজ্জামান
বাংলার প্রকৃতি তার আপন মহিমার সবটুকু যেন উজাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে প্রতিটি বাঙালি নরনারীর মনে-প্রাণে। ষড়ঋতুর বাংলাদেশে নানান ধরনের রূপ রস আর সুবাসিত সৌরভ আমাদের হৃদয় মনকে শিহরিত করে। প্রতিটি ঋতুর মাঝেই বাঙালি খুঁজে নেন বৈচিত্র্যময়তায় পরিপূর্ণ নানান উৎসব। তাই তো উৎসব প্রিয় বাঙালি প্রকৃতির আপন মহিমার...
Details

পুষ্টি নিরাপত্তা ও মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জিংক সার
ড. নির্মল চন্দ্র শীল১ ড. মোঃ আশরাফ হোসেন২
জিংক বা দস্তা এমন একটি অণুপুষ্টি যা উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহের জৈবিক ও বিপাকীয় কার্যাবলীর জন্য একান্ত অত্যাবশ্যক। পরিমাণে কম লাগে এ বিবেচনায় জিংককে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বললেও এর কার্যাবলী অনেক গুরুত্বপূর্ণ যা জীবসত্তার বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। আমাদের দেশের কৃষিতে জিংকের প্রয়োজনীয়তার কথা আশির...
Details
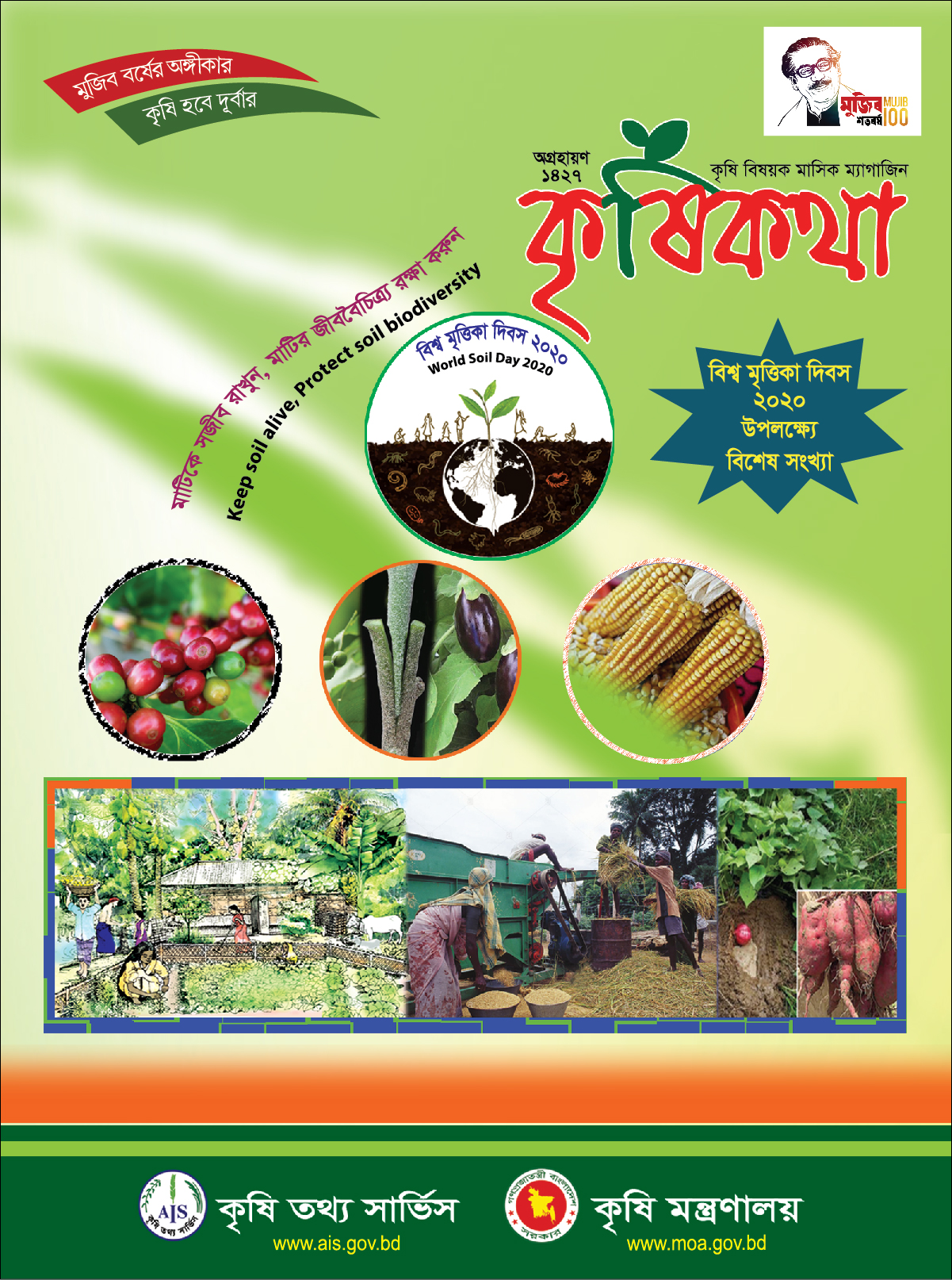
পৌষ মাসের কৃষি (কৃষিকথা অগ্রহায়ণ ১৪২৭)
(১৬ ডিসেম্বর-১৪ জানুয়ারি)
কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
হেমন্ত শেষ। ঘন কুয়াশার চাদর মুড়িয়ে শীতের আগমন। সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, আপনাদের সবার জন্য রইল শীতের শুভেচ্ছা। শীতের মাঝেও মানুষের খাদ্য চাহিদা নিশ্চিতে কৃষক-কিষানি ব্যস্ত হয়ে পড়েন মাঠের কাজে। মাঠের কাজে সহায়তার জন্য আসুন সংক্ষেপে আমরা জেনে নেই পৌষ মাসে সমন্বিত কৃষির সীমানায় কোন কাজগুলো আমাদের...
Details

প্রশ্নোত্তর (অগ্রহায়ণ) ১৪২৭)
কৃষিবিদ মো. তৌফিক আরেফীন
কৃষি বিষয়ক
নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য আপনার ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও রোগ দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করুন।
মোছাঃ আনজুআরা বেগম, গ্রাম: দক্ষিণ পাতাকাটা, উপজেলা: বরগুনা সদর, জেলা: বরগুনা
প্রশ্ন: ডালিয়া ফুলের পাতায় সাদা সাদা গুঁড়ার মতো আবরণ পড়ে। এ সমস্যা দূরীকরণে কী করব। জানালে উপকৃত হবো।
উত্তর : ডালিয়া ফুলের...
Details

কবিতা (অগ্রহায়ণ- ১৪২৭)
ভাসমান কৃষি কৌশল
ড. মোঃ আলতাফ হোসেন১
পানির উপরে ভাসমান কৃষি দেখতেই লাগে বেশ
আর সেই কৌশলটিই এখন জানিয়ে দিব সমগ্র দেশ।
দেশের অনেক এলাকাই দীর্ঘ সময় থাকে পানিতে নিমজ্জিত
তাই জন্য সেখানে মাটিতে কৃষি উৎপাদন করা যায় না ঠিকমতো।
ভাসমান কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় হাওড় ও উপক‚লবর্তী এলাকায়
বরিশাল, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ...
Details

স্বাধীনতা-উত্তর গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা
মো. কাওছারুল ইসলাম সিকদার
কৃষিই ছিল বাংলার আদি পেশা। এ অঞ্চলের মাটি, পানি তথা জলবায়ু ছিল কৃষির জন্য আদর্শ হিমালয়ের অববাহিকায় ভাটি অঞ্চলে বাংলার অবস্থান বিধায় অধিকাংশ নদী বাংলার উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। চীন, তিব্বত, নেপাল, ভুটান এবং ভারতের সীমানায় অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালার অসংখ্য হিমবাহের গলিত রূপ নদ ও নদীরূপে...
Details

মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি জোগানে ভুট্টার উপযোগিতা
ড. মো: মুজাহিদ-ই-রহমান১ ড. মোঃ এছরাইল হোসেন২
আদিকাল হতে বর্তমান সময়ের পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে খাদ্যাভাসের পরিবর্তনের প্রচেষ্টা যেন নিরন্তর। প্রায় দশ হাজার বছর আগে মেক্সিকোতে ভুট্টার চাষাবাদ শুরু হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের প্রধান খাদ্য হিসেবে ভুট্টা ব্যবহৃত হতে থাকে। বাংলাদেশে দানাশস্যের মধ্যে ধান ও গমের পরেই রয়েছে ভুট্টার অবস্থান।...
Details

সময়ের প্রাসঙ্গিকতা ও বঙ্গবন্ধু
কৃষিবিদ মো. মুকসুদ আলম খান (মুকুট)
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়, শৈশবে বাবা-মার আদরের খোকা এই বাঙ্গালির রাজনীতি করতে করতেই একদিন হয়ে ওঠে শেখ মজিব, শেখ সাহেব এবং মজিব ভাই। সময়ের পরিক্রমায় ১৯৬৯ এ হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। এই জাতির রাষ্ট্রীয় পরিচয় প্রাপ্তির জটিল ও...
Details

বাংলাদেশে কফি চাষের সম্ভাবনা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব
বাংলাদেশে কফি চাষের সম্ভাবনা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব
কৃষিবিদ কবির হোসেন১ কৃষিবিদ সাবিনা ইয়াসমিন২
পৃথিবীব্যাপী কফি একটি জনপ্রিয় পানীয়। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কনফারেন্স চলাকালে টি ব্রেক বা কফি ব্রেক বলে খ্যাত ছোট্ট বিরতির এই রেওয়াজ চালু হয়েছিল আমেরিকায় আঠারো শতকের প্রথম দিকে। চা বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করলেও...
Details

প্রতি ইঞ্চি জায়গা ব্যবহার করে বসতবাড়িতে সমন্বিত খামার
প্রতি ইঞ্চি জায়গা ব্যবহার করে বসতবাড়িতে সমন্বিত খামার
মৃত্যুঞ্জয় রায়
করোনাভাইরাস আমাদের নতুন করে অনেক কিছুই শিখিয়ে দিচ্ছে। অনেকেই বলছেন, করোনা যদি থেকেই যায় তো তার সাথে তো আমাদেরও থাকতে হবে। সারাক্ষণ এ রকম আতংক নিয়ে কি বাঁচা যায়? কিন্তু এটাও সত্যি, এ রকম ভয় যার মনে বাসা বাঁধবে করোনা তাকে মারার...
Details
















